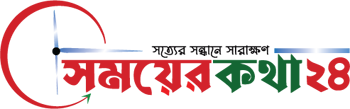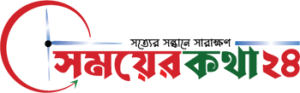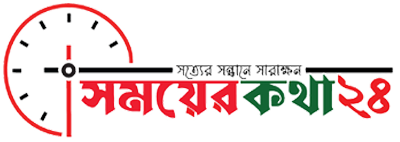একটি রাষ্ট্র কখনো দৃশ্যমান শত্রুর আবার কখনো-বা অদৃশ্যমান শত্রুর কবলে পড়ে। কূটনৈতিক কৌশল, সামরিক-বেসামরিক শক্তি দিয়ে মোকাবিলার চেষ্টা করে। কখনো বিজয়ী কখনো পরাজিত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ, ফলাফল ও প্রভাব অজানা কিংবা অদৃশ্যমান নয়। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ নিয়ে নানা শিবিরে বিভক্ত বোদ্ধারা। সুপেয় পানি, আধিপত্য কিংবা অন্য যা-কিছুই কারণ হোক না কেন পারমানবিক প্রযুক্তি কিংবা তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লব যে শতভাগ প্রভাবিত করবে তা অমোঘ সত্য। পুরো বিশ্ব কৌশলে নেতিবাচক মহাসড়কের একই রথযাত্রায় দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে ধ্বংস হওয়ার ইতিহাস বিমূঢ়। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এমন ইতিহাসে ধোঁয়াশার সাক্ষী আছেন ক’জন? তবে ভুল, বিকৃত, মিথ্যা তথ্য সম্বলিত কন্টেন্ট এর মাধ্যমে কীভাবে একটি সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিশ্বের ছাত্র, যুবরা বা অসচেতন সমাজের একটি বড়ো অংশ আসক্তির বেড়াজালে গোচরে- অগোচরে বিপদগামী কিংবা ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে তা দেখার জন্য দূরদর্শী বা বিশেষজ্ঞ হওয়া জরুরি নয়।
সঠিক বার্তা সম্বলিত একটি কন্টেন্ট দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী পৃথিবীর এক প্রান্তে ঘটে যাওয়া খবর অন্য প্রান্ত থেকে মানুষ সহজে স্বল্প সময়ের মধ্যে জানতে পারে। ইন্টারনেট তথা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের আশীর্বাদে বিশ্ব- ব্রম্মাণ্ড আজ বিশ্বগ্রাম (Global Village) এ রূপ ধারণ করেছে। তবে ভুয়া কন্টেন্ট বা খবর তেজী ঘোড়ার মতো দৌড়ায়। মেসির সতীর্থদের স্বর্ণের আইফোন দেওয়া, ট্রফিতে পা রাখায় মার্শের বিরুদ্ধে ভারতে এফআইআর দায়ের, গায়ক চার্লি পুথ বাংলাদেশে কনসার্ট করতে আসছেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস, পরীক্ষার রুটিন, সময়ে সময়ে ইত্যাদি অসত্য, বিভ্রান্তিমূলক আলোচিত ও রসালো খবর ইউটিউব, ফেসবুক, ম্যাসেঞ্জারসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয় কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে। কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগেই প্রচার হওয়ার সাথে সাথেই ব্যাক্তি, প্রতিষ্ঠান, সমাজ বা রাষ্ট্র বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। লক্ষ/কোটি ভিউয়ার। প্রচুর টাকা উপার্জনের সহজ প্রন্থা, মোক্ষম হাতিয়ার। নেতিবাচক বার্তার খবর মানুষ গ্রহণ করে বেশি। কারণ এতে সত্য-মিথ্যের রসবোধে মানুষের মধ্যে প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তবে সে নেতিবাচক বার্তার সত্যতা নিশ্চিত হওয়ার বালাই নেই কন্টেন্ট তৈরিতে। সাংবাদিকতার ভাষায় ‘ফ্যাক্ট চেক’ শব্দে কন্টেন্ট ক্রিয়েটর কিংবা দর্শকরা অভ্যস্ত নয়। ডিজিটাল ডিভাইসে একটি সত্য সংবাদ যত দ্রুত ছড়ায় অসত্য বা মিথ্যা সংবাদটি তার চেয়ে কয়েক’শ গুণ বেশি দ্রুত ছড়ায়। দর্শকের মান আর কন্টেন্ট ক্রিয়েটরের মান বা যোগ্যতা বা দক্ষতা খুব বেশি ব্যবধান নেই। সনদধারী ব্যক্তিরাও এসব কন্টেন্ট দেখে প্রতিক্রিয়া জানাতে শুনেছি। আরও বিপদজনক বিষয়ে হচ্ছে খোলামেলা যৌনতা বিষয়ে ছোট ছোট অজস্র কন্টেন্ট ফেসবুক কিংবা ইউটিউব খুললেই সামনে চলে আসে। খোঁজার প্রয়োজন হয় না। যা সামাজিক অবক্ষয়কে অতিমাত্রায় ত্বরান্বিত করছে বৈকি। ব্লাক মেইলিং, সাইবার ক্রাইম, বুলিং নিয়মিত অধ্যায়।
মিথ্যা, অসম্পূর্ণ, বিকৃত তথ্য সম্বলিত তৈরিকৃত কন্টেন্ট ফেসবুক, ইউটিউব, ম্যাসেঞ্জার, ইন্সট্রাগ্রামে সয়লাব। ব্যবহারকারীরা বুঝতেই পারেন না, কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা। যখন বুঝতে পারেন ততক্ষণে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যায়। অনেকে আবার বুঝার চেষ্টাও করেন না। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো বিশ্বব্যাপী ব্যবহার করা হয়। তবে শতভাগ শিক্ষিত দেশের নাগরিক এসব বিষয়ে আমাদের দেশের নাগরিকদের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন। বর্তমান নীতিমালায় বিশ্বের সবগুলো দেশের কিংবা কোনো বিশেষ এলাকার তথ্য ফেক্ট চেক করা ইউটিউব কর্তৃপক্ষের দ্বারা পুরোপুরি সম্ভব নয়। ইউটিউবের প্রধান সুসান ওজস্কিকে এ বিষয়ে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছে বিশ্বের অনেকগুলো দেশ, প্রতিষ্ঠান। সবার অনুরোধ হচ্ছে প্রতিদিনই ইউটিউবে বিভিন্ন বিষয়ে ভুয়া তথ্য ছাড়ানো হচ্ছে। বিশেষ করে যেসব দেশের ভাষা ইংরেজি নয়। যারা ইংরেজি ভাষায় কনটেন্ট তৈরি করে না তারাই ভুয়া তথ্য বেশি ছাড়ায়। ইংরেজি ব্যতিত অন্যান্য ভাষায় তৈরি কন্টেন্ট বুঝতে না পারায় মুছে দিতে অক্ষম কর্তৃপক্ষ। বিশেষভাবে অনুরোধক্রমে কর্তপক্ষ অনেক সময় ভুয়া কন্টেন্ট মুছে দেয়। সকল দেশের সকল অঞ্চলের ভাষা, সংস্কৃতি, ঘটনা প্রবাহগুলো ফেক্টচেক (Fact Check) করার জন্য ইউটিউব কর্তৃপক্ষ কতটুকু সক্ষম? তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। তবে ভুয়া, মিথ্যা তথ্যের বিকৃতির মাধ্যমে প্রতিনিয়তই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের নাগরিক, সরকার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিব্রত, বিপর্যস্ত, প্রতিারিত, অসম্মাননিত, হয়রানির সম্মুখীন হচ্ছে। ভিআইপিদের মৃত্যুর খবর, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, দুর্নীতি, অনৈতিক কর্মকাণ্ড, বাজারদর, সাম্প্রতিক ইস্যু নিয়ে অসংখ্যক ভুয়া, মিথ্যা কন্টেন্ট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সয়লাব। যুদ্ধ ক্ষেত্রে গুজব ছড়াতে, উস্কানি দিতে অশেষ দায়িত্ব পালন করছে। সর্বশেষ ২০২৪ সালে পার্বত্য অঞ্চলে ঘটে যাওয়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ভুয়া কন্টেন্টের ভূমিকা কারো অজানা থাকার কথা নয়। ইউটিউবের অ্যালগরিদম এ ক্ষেত্রে মিথ্যা কন্টেন্ট সনাক্তকরণে কতটুকু সক্ষম বা সফল তা বর্তমান পরিস্থিতি জানান দিচ্ছে। মূলত, নীতিবিবর্জিত লোকজনকে ইউটিউব কর্তৃপক্ষ প্লাটফর্মটিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ করে দিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের সদ্ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন ওঠে বারবার।
আন্তর্জাতিক ফ্যাক্ট চেকিং নেটওয়ার্ক স্বীকৃত বাংলাদেশের অন্যতম ফ্যাক্ট চেকিং বা তথ্য যাচাইকারী প্রতিষ্ঠান রিউমর স্ক্যানার ২০২৪ সালে ২ হাজার ৯১৯টি ভুল তথ্য সনাক্ত করেছে। ২০২৩ সালে এ সংখ্যা ছিলো ১ হাজার ৯১৫টি। এক বছরের ব্যবধানে ভুল তথ্য ছড়ানোর হার বেড়েছে প্রায় ৫২ শতাংশ। উল্লেখ্য যে, প্রকাশিত বা প্রচারিত সকল ভুয়া তথ্য উক্ত প্রতিষ্ঠানটি যাছাই করতে পেরেছে কি-না তা নিশ্চিত নয়। একটি কিংবা দুটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ফ্যাক্ট চেকিং করার বিষয়টি প্রত্যাশা করাও বোকামি। ফ্যাক্ট চেকিং নিয়ে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
মানুষ স্বভাবগতভাবেই লিখিত কোনো তথ্যের চেয়ে ছোটো আকারের ভিডিও দেখতে খুব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। ভিডিওতে চোখ এবং মস্তিষ্কের ব্যবহার একসাথে হওয়ায় অনেক বেশি মনোযোগ আকর্ষিত হয়। এছাড়া ছোটো আকারের কন্টেন্টগুলো দর্শকরা পছন্দ করে এবং সবচেয়ে বেশি ভিউ হয়। পক্ষান্তরে বড়ো কন্টেন্টগুলো সবাই এড়িয়ে যেতে চায়। স্বল্প সময়ে বেশি পরিমান ভিডিও কন্টেন্ট দেখা; সেটা আবার বর্তমান দর্শক প্রজন্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সকল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিশেষ করে ইউটিউব, ফেসবুক, টুইটার, মেসেঞ্জার কর্তৃপক্ষ বিশ্বের সকল দেশের ভাষা এবং সংস্কৃতি অনুযায়ী ফেক্ট চেক কর্মকর্তা নিয়োগ কিংবা এআই (Artificial Intelligence) ইন্সট্রুমেন্টের মাধ্যমে ফিল্টারিং এর মাধ্যমে ভুয়া কন্টেন্ট বা খবর বাতিল করা সময়ের দাবি। বিশ্বব্যাপী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্রার বিপ্লব ঘটতেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্রার মাধ্যমে সুপার এডিটিং এ সৃষ্ট আকর্ষণীয় মিথ্যা কন্টেন্টকে ঠেকাতে কিংবা সনাক্ত করতে সুপার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সর্বাধিক ব্যবহার অত্যাবশ্যকীয়। তাছাড়া ব্যবহারকারীরাও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে সচেতন হওয়া জরুরি। নির্ভরযোগ্য সূত্র ব্যতীত কোনো কন্টেন্ট বা খবরে বিব্রত হওয়া উচিত নয়। কন্টেন্ট ক্রিয়েটর থেকে শুরু করে দর্শক, ব্যবহারকারী সকলের স্মার্ট লিটারেসি (Smart Literacy) বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার জ্ঞান এখন অত্যাবশ্যকীয়। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিশ্বস্ত সংবাদ মাধ্যমগুলোর আরও জোরালো ভুমিকা এ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে পারে। এ ক্ষেত্রে যে সকল অ্যাপসের মাধ্যমে কন্টেন্ট প্রচার বা প্রকাশ করা হয়, সে সকল অ্যাপসে ফিল্টারিং বা ফ্যাক্ট চেক ব্যবস্থাও অসত্য বিভ্রান্তিকর কন্টেন্ট সনাক্ত তথা বাদ দেওয়ার একটি অন্যতম মাধ্যম হতে পারে। এতে করে এ সকল অ্যাপস ব্যবহারে সচেতন মানুষের আগ্রহ বাড়বে এবং বিশ্বস্ত ও জনপ্রিয় হবে। সম্প্রতি চীনা মালিকানাধীন জনপ্রিয় কন্টেন্ট অ্যাপস টিকটক নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের আদালত তা যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশেষ বিদায়ী সরকার মনে করেছে যে এতে রাষ্ট্রের নাগরিকদের নিরাপত্তা নানাভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। তবে বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সর্বশেষ নির্বাচনে ভোটের কথা চিন্তা করে টিকটকার পেশাজীবীদের পক্ষে একটি কৌশল এঁটেছিলেন। সেজন্য ভোটে টিকটকারদের নিরঙ্কুশ সমর্থনও পেয়েছিলেন। বর্তমানে সেটি যদি বাস্তবায়ন করতে চান তবে নিশ্চয়ই কিছু সীমাবদ্ধতা এবং কাঠামোর ভিতরে এনে নাগরিকদের টিকটক ব্যবহারের পথ সুগম করবেন বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। যা ফ্যাক্ট চেক বা নিরাপদ কন্টেন্ট কর্তৃপক্ষেরই নামান্তর হবে বলে মনে করছেন। এ পরিস্থিতিতে সরকারের মনিটরিং সেলগুলো এসব বিষয়ে আরও সোচ্চারের মাধ্যমে এমন দুর্বিষহতা থেকে দেশ, জাতি ও বিশ্বকে ভুয়া সংবাদ প্রবাহের বিপর্যস্ত স্রোত থেকে রক্ষা করতে পারে। ইউটিউবসহ সকল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কর্তৃপক্ষ নীতিমালা পরিবর্তন এবং প্রত্যেক রাষ্ট্র নিরাপদ কন্টেন্ট কর্তৃপক্ষ গঠন এখন সময়ের দাবি। প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বাংলাদেশের জন্য তা অত্যাবশ্যকীয়। এ বিষয়ে সরকার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে স্বাধীন স্বতন্ত্র কমিশন গঠন বর্তমান সময়ের অনুষঙ্গ।
লেখক:মোঃ বেলায়েত হোসেন
তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, খাগড়াছড়ি।
পিআইডি ফিচার